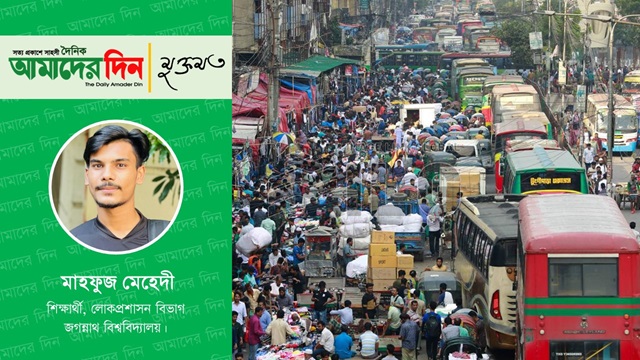মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কঠোর অবস্থানে সরকার

সাধারণ সময়ে শুধু ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের অধীন এলাকায় দৈনিক কমপক্ষে ৩০ থেকে ৩৫ টন মেডিকেল বর্জ্য উৎপাদন হয়। এর সঙ্গে করোনাকালে মাস্ক, গ্লাভস ও পিপিইসহ নানা সুরক্ষা সরঞ্জামের বর্জ্য যোগ হয়েছে। বিপুল পরিমাণ এই বর্জ্য পরিবেশসম্মত উপায়ে ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কর্র্তৃপক্ষের জন্য অনেকটাই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। আবার অনেক হাসপাতাল সিটি করপোরেশনের কাছে তাদের মেডিকেল বর্জ্য হস্তান্তর করতে চায় না। এমন পরিস্থিতিতে দেশের সব সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউটকে মেডিকেল বর্জ্য নিরাপদে বিনষ্ট ও শোধনের জন্য বেশ কিছু দিকনির্দেশনা দিয়ে অফিস আদেশ জারি করেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। এসব নির্দেশনা না মানলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।
গত ১৮ জানুয়ারি জারি করা ওই আদেশে বলা হয়, স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশ) আইন ২০০৯-এর ধারা ১১২ অনুযায়ী করপোরেশন এলাকায় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হলে সংশ্লিষ্ট করপোরেশন থেকে নিবন্ধন নিতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে আধুনিক পদ্ধতিতে নিজস্ব বর্জ্যরে ডিসপোজাল বা নিরাপদ ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। এসব বিধিবিধান না মানলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব (সিটি করপোরেশন-১) আ ন ম ফয়জুল হক দেশ রূপান্তরকে বলেন, ‘সারা দেশের সরকারি-বেসরকারি সব হাসপাতাল ও ক্লিনিককে নিরাপদ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দেশের সব সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাকে এ বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া স্বাস্থ্য বিভাগের কাছেও সারা দেশের সব হাসপাতাল-ক্লিনিকের তালিকা চাওয়া হয়েছে। মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তারা কী ধরনের ব্যবস্থা নেয় ও তাদের তদারকি সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিতে বলা হয়েছে।’
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চিকিৎসা বর্জ্যরে সঙ্গে করোনাকালে মাস্ক-গ্লাভসের মতো বর্জ্যও যোগ হয়েছে। চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় যেসব বর্জ্য তৈরি হয় তা মেডিকেল বর্জ্য হিসেবে ধরা হয়। তবে সাধারণ মানুষের ব্যবহার করা মাস্ক-গ্লাভস, পিপিই বা একই ধরনের অন্যান্য বর্জ্যকে মেডিকেল বর্জ্য হিসেবে ধরা হবে কি-না তা এখনো পরিষ্কার হয়নি। এ ধরনের বর্জ্যরে দুই ধরনের প্রভাব রয়েছে। একটি জনস্বাস্থ্যগত, অন্যটি পরিবেশগত। চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জনস্বাস্থ্যগত দিক লক্ষ করলে দেখা যাবে, এ বর্জ্যরে নিরাপদ বিনষ্ট ও শোধন না হলে পরিবেশগত ঝুঁকি তৈরি হয়। তাই বিনষ্ট ও শোধনের আগের কয়েকটি ধাপ যেমন বর্জ্য শনাক্ত করা, আলাদা করা ও পরিবহনের সঙ্গে জনস্বাস্থ্যগত ঝুঁকি যুক্ত থাকে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, তদারকি ও মনিটরিং প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।
বিশেষজ্ঞরা আরও বলেন, দেশে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ বা তদারকিতে খুব একটা নজর থাকে না। ফলে সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে বর্জ্য থেকে সাধারণ মানুষের সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের পরিবেশ প্রোগ্রাম মেডিকেল ওয়েস্ট বা হেলথ কেয়ার ওয়েস্টের জন্য একটি গাইডেন্স ম্যানুয়াল তৈরি করেছে। এ ছাড়া হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিগুলোর হাইজিন ম্যানেজমেন্টের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি ম্যানুয়েল রয়েছে। দুটি ম্যানুয়ালেই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি। সেখানে বলা হয়েছে এ ধরনের বর্জ্যকে ঝুঁকিহীন বর্জ্য (রিসাইক্লেবল ও বায়োডিগ্রেডেবল বর্জ্য), বিশেষ বর্জ্য (শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, রক্ত, রাসায়নিক), সংক্রমণক্ষম বর্জ্য, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ও অন্যান্য বর্জ্য হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. লেলিন চৌধুরী দেশ রূপান্তরকে বলেন, ‘চিকিৎসা বর্জ্য একটি বিশেষ বর্জ্য। এ বর্জ্যরে সঙ্গে রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে।’
করোনার সময় রোগীর বিছানা, চাদর, মাস্ক, গ্লাভস, পিপিই থেকে রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। করোনাকালে এ বর্জ্য শুধু হাসপাতাল নয়, বাসাবাড়িতেও বিপুল পরিমাণে তৈরি হচ্ছে। যেহেতু এসব বর্জ্য উৎসে আলাদা করা হয় না, ফলে মিশে গিয়ে সব বর্জ্য জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয় এবং বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।’
তিনি আরও বলেন, ‘সরকার এ বিষয়ে শুধু অফিস আদেশ জারি করে দিলেই দায়িত্ব শেষ নয়। কারণ হাসপাতালগুলোর পক্ষে নিরাপদ বর্জ্য ডিসপোসাল করা সম্ভব হবে না। এটির চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা করতে হবে সিটি করপোরেশন বা পৌরসভাকে। এখানে সরকার নির্ধারিত হারে ফি আদায়ের মাধ্যমে তা করতে পারে।’
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মাতুয়াইলে বর্জ্য বিনষ্ট ও শোধন করার জন্য একটি ইনসাইনেরেটর (চিকিৎসা বর্জ্য বিনষ্ট করার চুল্লি) রয়েছে। প্রিজম নামে একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকা ও এর আশপাশের হাসপাতালগুলো থেকে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করে সেখানে ইনসিনারেট করে। দেশের অন্যসব স্থানে এমন জায়গা নেই। আবার ইনসিনারেশন ব্যবস্থাপনার শেষ ধাপ। এতে মূলত পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাস করা যায়। কিন্তু এর আগের ধাপগুলোই জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ কীভাবে রোগীদের বা চিকিৎসাকর্মীদের বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, কীভাবে তা অন্য বর্জ্য থেকে আলাদা করা হচ্ছে, কীভাবে তা সংরক্ষণ করা হচ্ছে সেসব ধাপ।
ডিএসসিসির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ড. মো. সফিউল্লাহ সিদ্দিক ভূঁইয়া বলেন, ‘ডিএসসিসি এলাকায় মোট ১৪০০ মেডিকেল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার আমাদের কাছে বর্জ্য দিচ্ছে। আরও বেশ কিছু মেডিকেল প্রতিষ্ঠান এখনো চিকিৎসা বর্জ্য করপোরেশনের নির্ধারিত ভ্যানে দিচ্ছে না। আমরা প্রতিদিন প্রায় ১০ থেকে ১২ টন মেডিকেল বর্জ্য পাচ্ছি। এগুলো মাতুয়াইল ল্যান্ড ফিলিং স্টেশনে ডিসপোজাল করা হচ্ছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের এখনো পুরোপুরি সক্ষমতা তৈরি হয়নি। সব মিলিয়ে ৮০ শতাংশ বর্জ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে। অনেক প্রতিষ্ঠান নদীর ধারে অবৈধভাবে মেডিকেল বর্জ্য ফেলছে। তাদের চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া প্রতিটি ওয়ার্ডে এসটিএস নির্মাণ করার মাধ্যমে বর্জ্য সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা যাবে।’